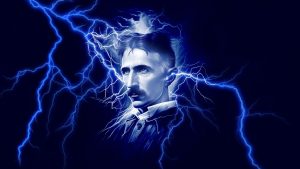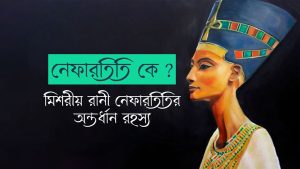পহেলা বৈশাখ বা পয়লা বৈশাখ (বাংলা পঞ্জিকার প্রথম মাস বৈশাখের ১ তারিখ) বঙ্গাব্দের প্রথম দিন, তথা বাংলা নববর্ষ।
এটি কেবল একটি তারিখ নয়, বরং বাঙালি জাতির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আনন্দ ও সাম্যের প্রতীক। যুগের পর যুগ ধরে এই দিনটি বাঙালিদের জীবনে নতুন আশার আলো নিয়ে আসে। নতুন বছরের প্রভাতে বাঙালি তার পুরনো গ্লানি, দুঃখ আর জরা ঝেড়ে ফেলে সেজে ওঠে নতুন সাজে, নতুন স্বপ্নে।
বাংলা নববর্ষের ইতিহাস
এক সময় নববর্ষ পালিত হতো ঋতুধর্মী উৎসব হিসেবে। কৃষিকাজ ঋতুনির্ভর হওয়ায় এ উৎসবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল কৃষির। তাই কৃষক সমাজের সঙ্গে বাংলা সন এবং নববর্ষের একটি আত্মিক সম্পর্ক গ্রথিত হয়ে আছে ঐতিহাসিকভাবে। কেননা, বাংলা সনের উৎপত্তি হয় কৃষিকে উপলক্ষ্য করেই।
বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ ঠিক কীভাবে ও কখন প্রচলিত হয়েছিল, তা এখনও একেবারে নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না। তবে নানান পরোক্ষ প্রমাণে এবং গবেষণায় মনে করা হয়, সম্রাট আকবর বাংলা সন প্রবর্তন করেছিলেন।বাংলা সনের প্রবর্তক নিয়ে সম্রাট আকবর বেশি আলোচিত হলেও, বাংলা পঞ্জির উদ্ভাবন ধরা হয় আসলে ৭ম শতকের রাজা শশাঙ্ক এর সময়কালকে। পরবর্তীতে সম্রাট আকবর সেটিকে পরিবর্তিত করেন খাজনা ও রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে।
পহেলা বৈশাখের সূচনা হয়েছিল মুঘল সম্রাট আকবরের শাসনামলে (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিঃ)। আকবর ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে বসেন। তিনি পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেন।
ভারতবর্ষে মোগল সম্রাজ্য পরিচালিত হতো, হিজরি পঞ্জিকা অনুসারে। আর হিজরি পঞ্জিকা চাঁদের উপর নির্ভরশীল। তখনকার দিনে কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করাটা ছিল একটি জটিল বিষয়। যেহেতু কৃষকদের কৃষি কাজ চাঁদের হিসাবের সাথে মিলতো না, তাই তাদের অসময়ে খাজনা দেয়ার সমস্যায় পরতে হতো। এই সমস্যা সমাধানে, সম্রাট আকবর রাজ্যজুড়ে কৃষিভিত্তিক নতুন একটি সন প্রবর্তনের আদেশ দেন। তখনকার বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও চিন্তাবিদ ফতেহউল্লাহ সিরাজী সম্রাট আকবরের আদেশে সৌর সন ও হিজরি সন এর উপর ভিত্তি করে নতুন সনের নিয়ম তৈরি করেন। আকবরের রাজত্বের ঊনত্রিশতম বর্ষ, অর্থাৎ ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি তারিখ-ই-ইলাহি বা ইলাহি নাম দিয়ে একটি অব্দ প্রচলন করেন, কিন্তু ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে এর প্রচলন হলেও এর গণনা দেখানো হয় ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ নভেম্বর থেকে(৯৬৩ হিজরি)থেকে । এই বছরই দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে যুদ্ধে তিনি(সম্রাট আকবর) সম্রাট হেমচন্দ্র বিক্রমাদিত্য(হেমু )কে পরাজিত করে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন বলে তা স্মরণীয় করে রাখতেই এ কাজ করা হয় বলে মনে করেন কেউ কেউ।
“তারিখ-ই-ইলাহি” পঞ্জিকায় মাসগুলোর নাম ছিলো করওয়াদিন, আরদি, ‘বিহিসু, খোরদাদ, তের, আমরদাদ, শাহরিয়ার, আবান, আজুর, দাই, বাহাম এবং ইস্কান্দার মিজ এমন নামে। আকবরের প্রচুর আশা থাকলেও, দিল্লি বা আগ্রায় “তারিখ-ই-ইলাহি” ব্যাপকভাবে করা সম্ভব হয়নি, তা কেবল চালু হয়েছিল আকবরের রাজসভায়।
ইলাহি সন প্রবর্তনের জন্য “আকবরনামায়” আকবরের যে ফরমান দেখা যায়, তাতে ইলাহি সন প্রচলনের নির্দেশ ছাড়াও ‘বিশুদ্ধ শুক্লপক্ষ পদ্ধতিতে’ পঞ্জিকা তৈরির নির্দেশ ছিল। নির্দেশ পাঠানো হয় সম্রাটের অধিরাজ্যের সকল পঞ্জিকাকার প্রণেতাদের নিকট। তারই ফলে হিজরি চান্দ্রবর্ষের সঙ্গে ভারতীয় সৌরবর্ষের সমন্বয়ে হিজরির রূপান্তরে বিহারসহ উত্তর ভারতে ফসলি সন, উড়িষ্যায় বিলায়তি ও আমলি সন এবং বঙ্গে সন বা বাংলা সন নামক পৃথক পৃথক আঞ্চলিক অব্দগুলি প্রচলিত হয় স্থানীয় পঞ্জিকাকারদের দ্বারা। আরবীয় হিজরি সন মহানবি মুহাম্মাদ (সা.)-এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত। সুপণ্ডিত সিরাজি সেই ঐতিহ্যকে আত্তীকরণ করে ১৫৫৬ সালে চলমান ৯৬৩ হিজরিকে গণ্য করেন ৯৬৩ বঙ্গাব্দ।
“বঙ্গাব্দের বা বাংলা সনের জন্মসন ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দ। মজার বিষয় হলো-জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা সনের বয়স দাঁড়ায় ৯৬৩ বছর; আর তার প্রচলন ঘটে আরও ২৯ বছর পর। বঙ্গাব্দের জন্মস্বভাব হচ্ছে কৃষক ও শস্য সংলগ্নতা। এ সহজাত স্বভাবের নিরিখে বাংলা সনকে বলা হয় ফসলি সন।”
দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অতীতের অধিকাংশ সৌর সনেরই বছর শুরুর দিন হয় বৈশাখ মাসে ১০-১৫ এপ্রিলের কাছাকাছি। কোনো রাজার রাজ্যাভিষেকের বছর ধরে যেসব সন গণনা শুরু করা হয় সেসব বছরে যেদিনই রাজার অভিষেক হোক না কেন, ঐতিহ্যের খাতিরে পঞ্জিকার শুরুর দিন অপরিবর্তিত রাখা হয়। আকবরনামা থেকে জানা যায়, ইলাহি সনের ফরমান জারির সময়ে বাংলায় লক্ষ্মণাব্দ চালু ছিল, যা সৌর বছর ছিল এবং যার বছরের শুরু হতো বৈশাখ মাসে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ফতেহউল্লাহ সিরাজী ১৫৮৪ সালে বাংলা অঞ্চলে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে পূর্বে আরোপিত হিজরি সনের পরিবর্তে ঐতিহ্যগত বাংলা পঞ্জিকা গ্রহণ করেন। এর ফলে বাংলা অঞ্চলে কৃষকদের খাজনা জমা দেবার মেয়াদ ৩ চান্দ্র মাস ও ১০ দিন বর্ধিত হয়।।
ফতেউল্লাহ সিরাজী চান্দ্রবর্ষ আর সৌরবর্ষের সমন্বয়ে সেকালে সুবে বাংলার জন্য যে ফসলি সন তৈরি করেছিলেন তা মূলত ফসল ঘরে ওঠার সময়কে কেন্দ্র করে। শীতকালীন ফসল বোনার মৌসুম কার্তিক মাস আর ফসল তোলার মৌসুম হলো মাঘের শেষ থেকে চৈত্রের প্রথম অবধি। এই সময়টাকে জমিদার জোতদাররা খাজনা তোলার সময়কাল হিসেবেও নির্ধারণ করে নেন। এর ফলে খাজনা আদায় সহজ হয় এবং বাংলা নববর্ষের সূচনা ঘটে।
ধারণা করা হয়, ফসল কাটার পর জমিদাররা প্রজাদের খাজনা মেটাতে উৎসব করতেন, মিষ্টিমুখ করাতেন — যা পরে ‘হালখাতা’ নামে জনপ্রিয়তা পায়। এই ইতিহাসই আমাদের আজকের পহেলা বৈশাখ উদযাপনের ভিত্তি তৈরি করে।
‘আইন-ই-আকবরী’ থেকে জানা যায়, সম্রাট এমন একটি ত্রুটিমুক্ত এবং বিজ্ঞানসম্মত সৌর সনের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, যা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্যই আদর্শ হবে। “তারিখ-ই-ইলাহি” ব্যাপকভাবে করা সম্ভব হয়নি, তা কেবল চালু হয়েছিল আকবরের রাজসভায়। বাংলা সনের মাধ্যমে তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছিল মনে করা যেতে পারে। কেননা, বাংলা যেমন ‘হিজরি সন’ নয়—তেমনি এটি ‘ইলাহী সন’ থেকেও ভিন্ন। হিজরি সনের উপর ভিত্তি করা হলেও এর গঠন পদ্ধতি ভারতীয় শকাব্দের মতো, অথচ এটি শকাব্দেরও সমগোত্রীয় নয়। শকাব্দের সঙ্গে এর সম্পর্ক এইটুকু যে, এর মাস ও দিনের নাম শকাব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে।
বাংলা মাসের নামকরণ
সুদূর অতীত থেকেই পূর্ব ভারতের পন্ডিতগণ জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ধারণা করা যায়, ষোড়শ মহাজনপদের যুগেই এই অঞ্চলে সৌর পঞ্জিকার উদ্ভাবন হয়। তবে স্থানীয় পূজা পার্বণ পূর্ণিমা, অমাবস্যা বা চান্দ্র মাস অনুযায়ী চলত। সে ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি পঞ্জিকা ছিল চান্দ্র-সৌর মিশ্রিত। ভারতীয় জ্যোতির্বিদরা সূর্য ১২টি মাসে যে যে নক্ষত্ররাশিতে অবস্থান করে সেই নক্ষত্ররাশির অবস্থানের ভিত্তিতে সূর্য পরিক্রমার হিসাব রাখতেন। কিন্তু তারা মাসগুলির নাম রাখেন চন্দ্রের গতিপথে পূর্ণিমায় যেসকল নক্ষত্র অবস্থান করে তাদের নামের ওপর ভিত্তি করে। যেমন, বিশাখা থেকে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা থেকে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়া থেকে আষাঢ়, শ্রবণা থেকে শ্রাবণ, ভাদ্রপদা থেকে ভাদ্রপদ (বাংলায় ভাদ্র), অশ্বিনী থেকে আশ্বিন, কৃত্তিকা থেকে কার্তিক, মৃগশিরা থেকে মার্গশীর্ষ (বাংলায় রোহিণী/অগ্রহায়ণী থেকে অগ্রহায়ণ), পুষ্যা থেকে পৌষ, মঘা থেকে মাঘ, ফল্গুনী থেকে ফাল্গুন এবং চিত্রা থেকে চৈত্র।